মুক্তিযুদ্ধ, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও বৈষম্যবিরোধী রাষ্ট্র সংস্কারের ভাবনা - খছরু চৌধুরী
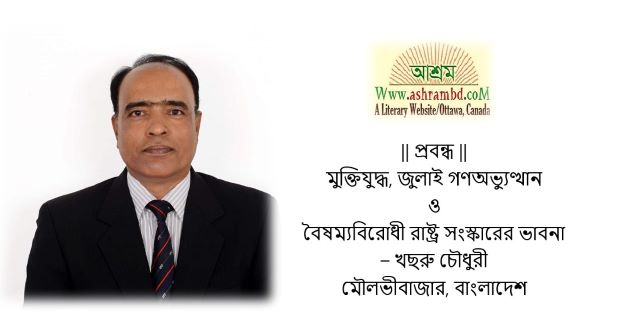
আধুনিক যুগের রাষ্ট্র ভাবনায় সংবিধান ও রাষ্ট্র এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংবিধান লিখিত বা অলিখিত যে রূপেই থাকুক, একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটির কল্পনাও করা যায় না। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার জুলাই ২০২৪'র গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরতন্ত্রের শীর্ষ নেতা শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এবং স্বাধীনতার ৫৩ বছর প'রে স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রের সংস্কার, সংবিধানের পরিবর্তন ইত্যাদি আলোচনা সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।
সংবিধানের সংস্কার নিয়ে আলোচনায় ঢুকার আগে বাঙালির জাতি পরিচয় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটু আলোচনা হওয়া দরকার। জাতি গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক সীমারেখা, একই ভাষা ও গড়পড়তা একই ধরনের সংস্কৃতির মেলবন্ধন অপরিহার্য ব'লে মনে করা হয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে এবং ইতিহাসের পেছনে গেলে ভারতবর্ষের বঙ্গাল অঞ্চলে (ছোট ছোট রাজ্য) সমতলে বসতি গড়া বাঙালিদের (অনার্য) তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার বছরের মোটামুটি কোথাও কোথাও স্পষ্ট এবং কোথাও কোথাও অস্পষ্ট ধরনের একটা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের জীবনাচার, ধর্ম ও সংস্কৃতি ছিল একেবারে নিজেদের মতো। পুরাণ কালে ভাষার লিখিত কোনো রূপ না-থাকলেও পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানে সকলে বাংলা ভাষার ব্যবহার করত, কথা বলতো। এই বঙ্গাল জনগোষ্ঠীতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনাচরণ নিয়ে গড়ে ওঠা ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্মের কোনোরূপ প্রভাব ছিল না। তখন পর্যন্ত সনাতন ধর্মের বর্ণবাদী নিয়মকানুন সম্পর্কে এই বঙ্গালরা ছিল অপরিচিত। ইতিমধ্যে, স্বাধীন জীবন-যাপনে অভ্যস্ত বঙ্গালদের মাঝে (অভিজাত বা আর্য সনাতনী ব্রাহ্মণদের ভাষায় চন্ড্রাল) বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এসে তাঁদের ধর্মের বিস্তৃতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন ব'লে জানা যায়। পরবর্তীতে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চল থেকে অভিজাত হিন্দু ব্রাহ্মণেরা আসেন এবং অনেকটা জোর করেই বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করিয়ে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য করেন। হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে বড় দূর্বলতা তথা নিষ্ঠুরতম দিক হলো ধর্মের ভিত্তিতে বর্ণবৈষম্য বা মানুষে মানুষে শ্রেণি বিভাজন। সমসাময়িককালে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একটা সংযোগ ঘটে। এই বাংলায় আরব, পর্তুগীজ, ডাচ বণিকদের আগমন ঘটে। পর্যায়ক্রমে মধ্য এশিয়া থেকে আগমন ঘটে সাম্রাজ্যবিস্তারী সেনাপতিদের। এরা ছিলেন ধর্মের পরিচয়ে মুসলিম। পূর্বদেশ বাংলা সহ সমগ্র ভারতবর্ষ-ই এসব বীরদের দ্বারা শাসিত হয়। একই সময়ে মধ্য প্রাচ্য থেকে মুসলমান সুফি দরবেশরাও আসেন, অপরাধ সংঘটিত করে নিজ দেশ-ত্যাগী অপরাধীরাও আসেন এবং ইসলাম ধর্মের বর্ণবৈষম্যহীন মহাত্ম্য প্রচার করেন। দীর্ঘ সময়ের নিপীড়িত নিম্নবর্গের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকেন। ধর্মপরিচয়ে মুসলিম মোগল শাসকেরা বাংলা সহ ভারতবর্ষ শাসনের সময়ে ইংরেজ বেনিয়াদের বাণিজ্য বিশেষ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অভিজাত এবং মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুরা এবং ক্ষমতা লিপ্সু মোগলদের একাংশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ষড়যন্ত্র করে ১৭৫৭ সালে ২৩ শে জুন পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাস্ত করে বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। পরাধীন হয় বাঙালি জাতি। হিন্দু মুসলমান পরিচয়ে ভাগ কর এবং শাসন করো (Divide and Ruled) নীতিতে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে প্রায় পৌণে দু'শ বছর শাসিত ও শোষিত হয় বাংলার হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী। অনেকটা ক্ষমতা হারানোর অভিমানে এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতিবাদে বিট্রিশ শাসনাধীন সময়ে ইংরেজদের দ্বারা চালুকৃত শিক্ষা গ্রহণ না-করায় বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায় অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। আধুনিক শিক্ষা বঞ্চিত হয়। নারী শিক্ষার প্রতিও উদাসীন হয়ে পড়ে। এরকম অপরিণত অভিমান ছিল মুসলিম নেতাদের বড় একটি ভুল। বাংলাসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে লড়াকু ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে ব্রিটিশরা ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে দু'টি স্বাধীন দেশে (ভারত ও পাকিস্তান) বিভক্ত করে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যায়। মহাকালের পরিক্রমায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এরকম ভাগাভাগির ভুলভ্রান্তি বিবেচনা করবে।
ধর্মের পরিচয়কে প্রধান করে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারত ও পাকিস্তান নামে যে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের মানচিত্র ও স্বাধীনতা এঁকে দিয়েছিল এর দু'অংশেই প্রাচীন বাঙালি জাতি ও তাঁদের বসবাসের স্থান (পূর্বদেশ) বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বিরোধের কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে কোনো অবস্থাতেই সমন্বয় করতে পারছিল না পূর্বপাকিস্তানের জনগণ। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের শাসন-শোষণে নানা ধরনের বৈষম্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও দরিদ্র শ্রেণির চাষাভুষার ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা কোনো শাসনামলেই রাজভাষার স্বীকৃতি ও রাজন্যদের পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। উপেক্ষিত থেকেছে রাজমহলের কাছে। নিজেদের দেশে, নিজেদের শাসনে নিজেদের ভাষার যুগ-যুগান্তরের অনুপস্থিতির ক্ষোভ এবং ইতিপূর্বে বাংলাভাষায় বরেণ্য সাহিত্যিকদের আবির্ভাব এবং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল বিজয় ছিল বাঙালির ভাষাভিত্তিক জাতিস্বত্ত্বার অদমনীয় পুনর্জাগরণ। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে অস্বীকার করলে জাতিসত্তার জাগরণের উপর নতুন এক আঘাত নেমে আসে। খামোশ হয় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ। উর্দুর প্রাধাণ্য ও পরবর্তী সময়ে শাসন ক্ষমতার বৈষম্য মেনে নিতে পারছিল না। বাংলার ছাত্র সমাজ অগ্র সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। শুরু হয় বাঙালির অধিকার ভিত্তিক আন্দোলন। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সচেতন এবং অবচেতনভাবে বাঙালির ভাবমানসে জাতিস্বত্ত্বার বীজ বেড়ে উঠতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ৪ টা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করা ছাত্র লীগ এবং ১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করা ছাত্র ইউনিয়ন বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা প্রচার-প্রসার ও জাগ্রত করার সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল হিসেবে মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টী ও ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টীও অসামান্য অবদান রাখে। ঐতিহাসিক সমাজ বিকাশের বিয়মে ইতিহাসের নতুন বাঁকে বাঁকে নতুন নতুন নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। ছাত্র-জনতার রাজনৈতিক লড়াই সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তৎকালীন ছাত্র লীগের নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্খা দ্রুততর সময়ে বিকশিত হয়। ছাত্রলীগের ভেতরে গড়ে তোলা হয় 'নিউক্লিয়াস' নামে নতুন সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মানের এক চিন্তাশীল সত্তা— যে সত্তার প্রতিষ্ঠা-পরিচালনায় ছিলেন তৎকালীন ছাত্র লীগের নেতা সিরাজুল আলম খান। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করলে এটুকু বুঝা যায় যে, নিউক্লিয়াসের ছাত্রনেতারা পূর্বপাকিস্তানের ছাত্র-শ্রমিক-জনতাকে স্বাধীনতার প্রথম স্বপ্ন দেখায় এবং ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে জনগণের অধিকারের দাবির সংযোগ ঘটায়। ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, আওয়ামী লীগ এর ৬ দফা এবং ছাত্র সমাজের ১১ দফায় পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত ও বৈষম্য পীড়িত মানুষের শোষণ মুক্তির আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটায়। পাকিস্তানের ধনিক শ্রেণির মাত্র ২৪ বছরের শাসনে অর্থনীতির নিয়মেই ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে তোলা জাতীয়তাবাদের অপমৃত্যু ঘটে এবং সর্বস্তরের জনগণের চেতনায় বিকল্প হিসেবে স্থান দখল করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি ধনিক শ্রেণির দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে চলে আসে এবং ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান আবির্ভূত হয়ে জনগণ-মন-অধিনায়ক হৃদয়ে একচ্ছত্র দখল নিতে সমর্থ হোন। ইতিহাসের নিক্তির বিচারে শেখ মুজিবকে বাড়িয়ে রাখা বা কমিয়ে রাখার কোনো সুযোগ নেই। তিনি যা আছেন তা-ই থাকবেন।
পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর শোষণ বৈষম্যের বিবেচনায় কমিউনিস্টরা জনগণের মনে স্থান নিতে ব্যর্থ হলে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি ধনিক শ্রেণির দল হলেও জনগণের আস্থায় চলে আসে। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্বপাকিস্তান অংশে একচ্ছত্র সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জন করে। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভূট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও জাতীয় পরিষদের ৩১০ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭ আসন লাভ করে সরকার গঠনের জন্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জনগণের ভোটের রায়ে নির্বাচিত দলকে ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা টালবাহানা শুরু করে পাকিস্তানের সরকার ও মিলিটারী ব্যুরোক্রাসী। 'বাঙালিদের শাসন মেনে নেওয়া যায় না' বলে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে বাঁধ সাধেন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানেরা সহ পশ্চিম পাকিস্তান অংশের জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলি ভুট্টো। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর নির্বাচনে বিজয়ের পর থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিটি দিন ছিল বাঙালির আড়াই হাজার বছরের অধিকার আদায়ের লড়াই সংগ্রামের শ্রেষ্ঠতম সময়। এই ইতিহাস চাইলেই কেউ মুছতে পারবে না, বিকৃত করতে পারবে না — শাসকদের চেষ্টায় সাময়িক বিকৃতি হলেও স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে সঠিক ইতিহাস-ই ফিরে আসবে বারে-বারে। কারণ এটা ছিল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। এখন গভীর বিচার বিশ্লেষণ নিয়ে বুঝা উচিত, বাঙালির 'মুক্তিযুদ্ধটা' আসলে কেমন ধরনের যুদ্ধ ছিল? ইহার পরিচালন পদ্ধতির ও নিয়ন্ত্রণ কোন শ্রেণির হাতে ছিল? যুদ্ধকালীন সময়ে বিশেষভাবে স্মরণীয় দিনগুলো কি কি? যুদ্ধকালীন সময়ের যৌথ-নেতৃত্ব কারা?
পাকিস্তানি সেনা-শাসকেরা ক্ষমতা হস্তান্তরের নামে আলাপ-আলোচনার নাটকীয়তা করে মূলত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্বপাকিস্তানে আধুনিক মারণাস্ত্রের মজুদ সংহত করার কৌশল নেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা নানা কর্মসূচি পালন করতে থাকেন। জাতীয় সংসদের নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে ১ লা মার্চ থেকে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু। ২ রা মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বট তলায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে ছাত্রনেতা আ স ম আব্দুর রব বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বিকেলে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি সহ ঢাকার অনেক বাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেন ছাত্র লীগের নেতারা। ৩ রা মার্চে রমনা রেসকোর্স ময়দানে (সরওয়ার্দী উদ্যান) 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র নেতৃত্বে (যেটি ১৯৬২ সাল থেকে গোপনে ছাত্রলীগের ভেতরে কাজ করে আসছিল) স্বাধীনতার 'ইশতেহার' পাঠ করেন তৎকালীন ছাত্রনেতা শাহজাহান সিরাজ। এই ইশতেহার পাঠ অনুষ্ঠানেই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের পক্ষ থেকে সারা পূর্বপাকিস্তানের জনসাধারণের মাঝে প্রচার চালানো হয় যে, ৭ মার্চ সরওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা করে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন। জনসভাকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভ। জনজাতির নতুন রাষ্ট্রের প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে সর্বস্তরের জনগণ। জনশ্রুতি রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পায়ে হেটে ও নানাভাবে ৭ মার্চের জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রাশ ২০ লাখ মানুষ। জনসভায় বঙ্গবন্ধুর জবানীতে পাঠ করার জন্য সিরাজুল আলম খানের ড্রাপ্ট করা বক্তৃতায় ছিল কবিতার মতো প্রাণ-ছোঁয়া শব্দ চয়ন — যা আজ ইউনেস্কোর স্বীকৃতিতে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ নিয়ে নানা ধরনের বিচার বিশ্লেষণ কিংবা গবেষণাও হতে পারে। কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় আমার ধারণাটি হচ্ছে (১) এই ভাষণের পর আমজনতার কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা বলে আলাদা কোনো নির্দেশ দানের প্রয়োজন হয় না। কারণ যুদ্ধ বাঁধলে জনগণ কি করতে হবে, উক্ত ভাষণে ইহার সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল, (২) কিন্তু তখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের ক্ষমতা প্রাপ্তির আশায় দোদ্যুলমান ছিলেন। যে কারণে স্বাধীনতা অর্জনে ছাত্র লীগের নিউক্লিয়াস নেতৃত্বের যৌথ সিদ্ধান্ত হলেও, আওয়ামী লীগ দলগতভাবে তদ্রূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। পাক আর্মি ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ কাল রাতে 'অপরেনশন সার্চ লাইট' দ্বারা পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম গণহত্যা (Genocide) করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও ঢাকার অন্যন্য জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায়। ২৬ মার্চ ভোর বেলা গ্রেফতার করে বঙ্গবন্ধুকে। ধর্ম-বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে যাকে পেয়েছে তাঁকেই হত্যা করছে। নিরস্ত্র বাঙালির ওপর এরূপ আকস্মিক হত্যাকান্ড দেখে বিস্মিত হয়েছেন গোঠা দুনিয়ার গণতান্ত্রিক বিবেকবোধ সম্পন্ন মানুষ। বাঙালি জাতির ওপর পাকিস্তানিদের চাপিয়ে দেওয়া এই যুদ্ধের চরিত্র জনযুদ্ধের রূপ ধারণ করে। কেউ কারো নির্দেশের অপেক্ষা না-করেই স্ব-স্ব অবস্থান থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করে। যুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তানিদের নানা প্রপাগাণ্ডার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ইসলাম বিদ্বেষী, ভারতের দালাল, হিন্দু ও রাষ্ট্রবিরোধী কমিউনিস্ট নিধন। এগুলো হালে পানি পায়নি। যুদ্ধটা দ্রুত গতিতে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক- পুলিশ-ইপিআর-সেনাবাহিনী-সরকারি পেশাজীবি-শিক্ষক সহ সর্বাত্মক ছড়িয়ে পড়তে কোনো অসুবিধাই হয়নি।
গণহত্যার সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে, ২৬ মার্চ ভোরবেলায় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন এবং চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান এর কাছে ওয়ারলেস মেসেজে এই ঘোষণার বার্তা প্রেরণ করেন (মুক্তিযুদ্ধের গবেষকদের মধ্যে এনিয়ে মতের ভিন্নতা আছে)। ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান প্রথমে তাঁর নিজের নামে এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন (এমন মতামত নিয়েও মতের ভিন্নতা আছে)। এদিকে, ২৫ মার্চ সন্ধ্যা রাতে বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের অনেক নেতাদেরকে আত্মগোপনে যাবার পরামর্শ দেন। বঙ্গতাজ তাজ উদ্দিন আহমদ সহ দলের অনেক সিনিয়র নেতারা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক পরবর্তী নির্দেশনা না-পেয়ে বিফল মনোরথে যাঁর যাঁর গন্তব্যে/ আত্মগোপনে চলে যান। আওয়ামী লীগ এর সিনিয়র নেতা তাজ উদ্দিন আহমদ গণহত্যার খবর শুনে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন! কী করবেন আর কী করবেন না — যুগস্রষ্টার রাজনৈতিক ভাবনার অনকগুলো অংক মেলাতে লাগলেন। অংক মিলে গেল। পাকিস্তানীদের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে। এখনই স্বাধীন বাংলাদেশে জন্য বিপ্লবী সরকার গঠন করতে হবে। তাঁর সাথে আত্মগোপনে সাথে থাকা ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম এবং কাছাকাছি অবস্থান করা আওয়ামী লীগ এর নেতাকর্মীদের কাজে লাগালেন। সবাই মিলে নির্বাচনে বিজয়ী পূর্ব পাকিস্তানের এমএনএ ও এমপিদের কুষ্টিয়া জেলাতে আসার খবর দিলেন। আওয়ামী লীগ-সহ স্বাধীনতাকামী অন্যান্য দলকেও একই সংবাদ দেওয়া হলো। ১০ এপ্রিল পর্যন্ত ১৫ দিনে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের ভবের পাড়া বৈদ্যনাথ তলার আম বাগানে ১৬৭ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির ৮ থেকে ১০ জন উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যোগাযোগের কঠিন অবস্থা মেনে নিলেও এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আলোচনা করার দাবী রাখে। ২৫ মার্চের গণহত্যার পর থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাক আর্মির বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত জনপ্রতিরোধ গড়ে ওঠছে, কোথাও কোথাও অকাতরে জীবন দিচ্ছে স্বাধীনতাকামী জনতা, নেতৃত্বে নিউক্লিয়াসের তরুন ছাত্র-যুবক। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় দল আওয়ামী লীগ-এর দলগত কোনো সিদ্ধান্ত না-থাকা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পাকিস্তানের এমএনএ, এমপি হওয়াতে উনাদের বেশিরভাগই পাকিস্তান ভেঙে 'স্বাধীন বাংলাদেশ' গঠনে সন্ধিহান ও দোদুল্যমান ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতে তাজ উদ্দিনের ডাকে এমন নগন্য সংখ্যক জনপ্রতিনিধির উপস্থিতি এটি প্রমাণ করে। রাজনীতিতে বিচক্ষণ, দেশপ্রেমে পরীক্ষিত দূরদর্শী নেতা তাজ উদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন গ্রুপের উপদলীয় কোন্দল উপেক্ষা করে এবং অন্যান্য দলমতের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের উপস্থিতিতে ১৭ এপ্রিল মুজিব নগর (মেহেরপুর) সরকার গঠনে সমর্থ হোন। মুজিব নগর সরকারের রাষ্ট্র প্রধান করা হয় পাকিস্তানের জেলে বন্দী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সরকার প্রধান হয়েছিলেন বঙ্গতাজ তাজ উদ্দিন আহমদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের নানা ঘটনা প্রবাহ দিবসের বিবেচনায় '১৭ এপ্রিল' এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিবস আর কোনটি হতে পারে?
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির জনযুদ্ধ। জনযুদ্ধ পরিচালনায় 'স্বাধীন বাংলাদেশ' সরকার গঠন করা হয় এবং এই সরকারের নেতৃত্বেই চীন, আমেরিকার মতো পরাশক্তির চরম বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেশী ভারত, পরাশক্তি রাশিয়া-সহ পৃথিবীর মুক্তিকামী জনতার অকুন্ঠ সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। ১৬ ই ডিসেম্বর'১৯৭১ এ দেশ স্বাধীন হয়, ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (কোনো দপ্তরে বসে নয়) পাকিস্তানিরা ভারত- বাংলাদেশের যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আসার পথে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর প্রধান এম এ জি ওসমানীর হেলিকপ্টার হামলার শিকার হয়েছিল এবং তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। ঘটনার কোনো তদন্ত করা না-হলেও মনে করা হয় এই হামলাটি ভারত করেছিল। কেন করেছিল? স্বাধীন বাংলাদেশে এ প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে এরকম গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঘটনা রয়েছে, যা স্বাধীন বাংলাদেশে আলোচনা হয়নি, গবেষণাও হয়নি। ১০ জানুয়ারি ইংল্যান্ড ও ভারত হয়ে বঙ্গবন্ধু দেশে আসেন। ভারতের মাটিতে পা-রেখেই দুঃসাহসের সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার সৈন্য বাংলাদেশ থেকে কবে সরাবেন....? দেশে এসেই তিনি সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিন আহমদকে জানিয়েছিলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে চান....। একটা স্বাধীন দেশের বিপ্লবী সরকার, যে সরকার তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) মতো একজন মহীরুহ রাজনৈতিক নেতার অনুপস্থিতিতেই দেশটাকে স্বাধীন করেছেন। সেই সরকারকে সাইড/বাতিল করে তিনি (বঙ্গবন্ধু) পাকিস্তান শাসনের জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিয়ে সরকার গঠন করেছিলেন — এটি কেন করা হয়েছিল ইহার পূর্ণাঙ্গ বিচার-বিশ্লেষণ এদেশে হয়নি। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, আওয়ামী লীগ পাকিস্তান আমল থেকেই লুটেরা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পূর্বপাকিস্তানের পিছিয়ে পড়া শিল্পপতিদের ভরসা ও আস্থার স্থান দখল করেছিল। পাকিস্তানের২২ শিল্প পরিবারের ২০ পরিবার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। জাতীয়তাবাদী লড়াই সংগ্রামে উঠতি বুর্জোয়াশ্রেণীকে অস্বীকার করার করার উপায় নেই। জাতিগত শোষণ বৈষম্যের শিকার জনগণের আকাঙ্খার সাথে সংহতি জানিয়ে কমিউনিস্টরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে জাতীয়তাবাদী সকল লড়াই সংগ্রামের মূল স্পিরিট আওয়ামী লীগ-ই ধারণ করতে সক্ষম হয়। কমিউনিস্টরা মূল নেতৃত্বের জায়গা থেকে ছিটকে পড়েন। আওয়ামী লীগ এর ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ এর নিউক্লিয়াস সৃষ্ট স্বাধীনতাকামী ধারায় শোষণ মুক্তির আকাঙ্খা স্পষ্ট থাকলেও মূল দলের নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রণে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণির। বাংলাদেশ যে ধণিক শ্রেণি সমর্থিত বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে স্বাধীন হয়েছে — এই সত্য অস্বীকার করার কোনো যুক্তি বা তত্ত্ব আছে কি? আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল হলেও দলের শ্রেণি-চরিত্র-ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ৯ মাসের লাখো শহীদের রক্তদান, আড়াই লাখ নারীর সম্ভ্রমহানির ত্যাগ ও জনযুদ্ধে জীবন বাজিরাখা মুক্তি সেনাদের শোষণ মুক্তির জাগ্রত আকাঙ্খাকে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে গেছে। গণমুক্তির আকাঙ্খা ও লক্ষ্য নিয়ে পথচলা 'স্বাধীন বাংলাদেশ' সরকারের অঙ্গীকার দূর্বল করার প্রথম প্রয়াসই ছিল পাকিস্তান শাসনের জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও পাকিস্তানের সেটআপকৃত আমলাতন্ত্র বহাল রেখে রাষ্ট্র পরিচালনার বন্দবস্ত করা। যদিও দক্ষ আমলাতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রযন্ত্র অচল। কিন্তু অদক্ষ ও লুটেরা রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় গণবিমূখ আমলাতন্ত্র কখনো কখনো পেন্টাগনের চেয়ে শক্তিশালী দানবের ভূমিকা পালন করে। দেশের স্বাধীনতার জনযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীর অবিস্মরণীয় ভূমিকা রয়েছে। তাই ব'লে একজন বেসামরিক যোদ্ধাও কি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত হবার যোগ্য ছিলেন না? স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ঘাটলে হবিগঞ্জের জগৎজ্যোতি-সহ অন্তত কুড়িজন মুক্তিযোদ্ধা পাওয়া যাবে যাঁদের প্রত্যেকেই বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে সম্মানিত হবার উপযুক্ত ছিলেন। বিষয়টি হলো, পাকিস্তান মানসিকতার আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষ বাছাই প্রক্রিয়ায় বাঁধ সেধেছে এবং জনযুদ্ধ সংগঠনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও মুক্তিযোদ্ধার অবদানকে শ্রেণি ও গোষ্ঠীর স্বার্থে কুক্ষিগত করা, ক্ষেত্র বিশেষে বিতর্কিত করার প্রয়াস চালিয়েছে। কার্যত স্বাধীন ভূখণ্ড, পতাকা ও জাতীয় সংগীত-ই ছিল জনগণের মুখ্যপ্রাপ্তি; বৈষম্য নিরসন, শোষণ মুক্তি ও গণতন্ত্র নয়। ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কি এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে না? দেশের বাম ও ডান পন্থার ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও নেতৃত্বদানকারী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের আর্থসামাজিক অবস্থান আজ অবধি নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। শাসক বুর্জোয়া লুটেরা পুঁজিপতি শ্রেণির বিভাজনের রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচে আবদ্ধ রয়েছেন। ফলে, স্বাধীন দেশের রাজনীতিতে ভারতপন্থী ও পাকিস্তান পন্থীদের প্রকাশ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং এ দু'টি শিবিরে বিভক্ত জনগণের মাঝে বাংলাদেশ পন্থী রাজনীতির ধারা এগিয়ে নেওয়ার মতো দক্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখনো অনুপস্থিত।
মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনে অবদান রাখা ব্যক্তিবর্গের নির্ধারিত করণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের বিশেষ দিনগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতিদান একটি জাতির জাতিগত-চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে, ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করে। স্বাধীনতার পরবর্তী ৫৩ বছরের শাসকগোষ্ঠী কী এই দায়িত্ব পালনে নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন? মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচির জন্য সকলেই নিজের মতো বয়ান লিখিয়েছেন বা বদলিয়েছেন — নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনের সদিচ্ছা কোনো সরকারের ছিল ব'লে মনে হয়নি। স্বাধীনতার কে 'জনক' আর কে 'ঘোষক' — এই দ্বন্দ্ব দেখতে-দেখতে একটি প্রজন্ম বড় হয়েছে। এর প'রের প্রজন্মটি দেখেছে, কর্তৃত্ববাদী শাসনে নিরর্থক স্বাধীনতার স্বরূপ ও চেতনার ব্যবসা। এমন অবস্থায় তরুন প্রজন্মের অনেকেই জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানকে 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' বলতে দ্বিধা করছেনা। যে দেশের ইতিহাস চর্চায় ১৭ এপ্রিল অর্থাৎ 'স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের' শপথ গ্রহণের তাৎপর্যপূর্ণ দিবসটিও যখন রাষ্ট্রীয় দিবসের মর্যাদা পায়না, ২ রা মার্চ জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস, ৩ রা মার্চ স্বাধীনতার ইসতেহার পাঠ দিবস রাষ্ট্রের গৌরব গাঁথায় থাকে না — সে দেশের রাষ্ট্রীয় দিবসগুলো জনগণের মনে গ্রহণযোগ্য হবে কি করে? সম্প্রতি বর্তমান ইন্টেরিম সরকার রাষ্ট্রীয় দিবসের তালিকা থেকে যেগুলো বাতিল করেছেন সেগুলো হলো ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ৫ আগষ্ট শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী, ৮ আগষ্ট শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী, ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস, ৪ নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস এবং ১২ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস।
বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সুলিখিত সংবিধন রয়েছে। নাগরিক সমাজের কয়জন এটি পড়েছেন বা পড়ার সুযোগ পেয়েছেন তা জানিনে। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের অধিকাংশ কর্মচারী যে এটা পড়েননি — তা তাদের মালিক জনগণের সেবার ধরণ দেখলে বুঝা যায়। ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ পরিচালনা করার জন্য এই সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছিল। যেটিকে ৭২ এর সংবিধান নামেই অভিহিত করা হয়। শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে এটিকে কাটাছেঁড়া করেছেন ১৭ বার। সংবিধানটিতে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি আছে ঠিকই কিন্তু অধিকারের সুরক্ষায় রাষ্ট্র ব্যর্থ হলে, রাষ্ট্রকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর সুযোগ নেই। অর্থাৎ খাদ্য আপনার মৌলিক অধিকার কিন্তু আপনি না-খেয়ে মরলেও রাষ্ট্রকে দায়ি করতে পারবেন না। তদ্রূপ শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদিও। সংবিধানে সভা সমাবেশ করার মতো গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সংসদে দাঁড়িয়ে ফ্লোর ক্রসিং বক্তৃতায় সদস্য পদ চলে যাবার বিধান নির্ধারিত। সংবিধান ইহার স্বীয় বৈশিষ্ট্যগুণেই শাসককে স্বৈরাচারী হতে উৎসাহিত করে। সামাজিক বৈষম্য নিরসনের সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই। সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ রয়েছে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং একই সাথে মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সংযোজন থাকায়, এটি একটি গোঁজামিলের দলিল রূপে ঠিকে আছে। এটি ১৯৭১ এর মহান স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে জাগরিত হওয়া জনগণের মুক্তির আকাঙ্খা যেমন ধারণ করতে ব্যর্থ, তেমনি ১৯৯০ ও ২০২৪ এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের বৈষম্যহীন রাষ্ট্রের আকাঙ্খাকেও ধারণ করতেও অক্ষম। যে কারণে জুলাই-আগষ্ট গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করেই রাষ্ট্র সংস্কার করতে হবে। সংস্কার মানে সংবিধান-সহ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের অধীনে থাকা গণপ্রতিষ্টান সমূহের সংস্কার। সংস্কার ব্যতিরেখে এই রাষ্ট্রের চরিত্র যে গণমুখীন হবে না, এটা তো বিগত ৫৩ বছরের শাসনে প্রমাণিত হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধানের অধীনেই তো এই রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণের সাথে এমন কোনো দূর্ব্যবহার নেই যা করেননি। তাদের আচার-আচরণে কিছু বিষয় খেলো প্রকৃতির ও হাস্যকর হলেও মূলত দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও চেয়ারে বসে যা ইচ্ছে তা করার মানসিকতা লালন করত। পরিণতিতেই স্বৈরাচার সৃষ্টি করতো। বিষয়টি স্পষ্ট করতে তিনটি উদাহরণ দেই। (১) হাসিনার ১৫ বছরের শাসনে প্রজাতন্ত্রের কাজের সন্তোষ্টির স্বীকৃতি স্বরূপ যে সকল আমলাকে জাতীয় 'শুদ্ধাচার পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে তাদের ৯৯ ভাগই করাপ্টেড। (২) ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে মাঠের অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনতাকে ইউএনও শপথ করাচ্ছেন, "আমি ঘুষ খাবো না, ঘুষ দেবোও না......।" অথচ, সে নিজেই যে ঘুষ খায়, শপথকারী জনগণ তা বলার সাহস বা অধিকার ছিল না। (৩) ঘুষখোর অফিসারদের অফিসে অফিসে ঝুলানো সাইনবোর্ড (এখনও হয়তো আছে) 'আমি এবং আমার এই অফিস ঘুষ দূর্নীতিমুক্ত'। সকলের মনে রাখা উচিত যে, এ ধরণের তামাশাভরা আচরণ করা হয়েছে, বর্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে। সুতরাং ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এই শাসনতন্ত্রের সংস্কার ছাড়া এ জাতির মুক্তি নেই। ২৯ অক্টোবর ২০২৪, মৌলভীবাজার।।
খছরু চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক, লীলা নাগ স্মৃতি পরিষদ, মৌলভীবাজার ও সদস্য সচিব, হাওর কাউয়াদিঘী রক্ষা আন্দোলন, মৌলভীবাজার।
লেখা তৈরীর সহযোগি গ্রন্থ ও ব্যক্তি: বাংলাদেশ দর্শন, মুক্তিযুদ্ধের দলিল, ডক্টর মুহাম্মদ জাফর উল্ল্যার সমকালে প্রকাশিত লেখা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মোতাহার হোসেন ও শাহেদ বখত ময়নু'র সাথে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলাপচারিতা।।
-
নিবন্ধ // মতামত
-
29-10-2024
-
-